অমর মিত্রের উপন্যাস: ও আমার পছন্দপুর । নাহার তৃণা
‘মেলার দিকে ঘর’ ছোটো গল্প প্রকাশের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখেন। সালটা ছিল ১৯৭৪। এরপর লেখক হয়ে ওঠার পথপরিক্রমায় যেসব বাঁধাবিঘ্ন পথরোধ করে দাঁড়াতে চেয়েছে, দূরদর্শিতা এবং নিরলসভাবে লিখে যাওয়ার অন্তর্গত তাগিদ সেসব ঠেলে তাঁকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁর ‘পেন্সিলে লেখা জীবন’ এর ধারাভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁর মতো নবীন এক লেখকের সাথে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাশকের রূঢ় আচরণের বয়ান। সেই সময় যদি তিনি আবেগের আবর্তে ভেসে গিয়ে হটকারী সিদ্ধান্ত নিতেন, সাহিত্যের পৃথিবীতে তাঁর ভ্রমণটা হয়ত সুখকর হতো না। কণ্টকপূর্ণ হয়ে পড়তো সে যাত্রা। আমাদের সৌভাগ্য সেরকমটা হয়নি। বলছি, সত্তর দশক পরবর্তী সময়ের শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের কথা। তাঁর লেখালিখির রয়েছে বিশাল জগৎ। সত্তর ছুঁইছুঁই বয়সেও যা দারুণ গতিতে চলমান। ছোটোগল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, প্রবন্ধ নিয়মিত লেখালিখির পাশাপাশি ওয়েবজিন ANTONYM এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি দারুণ দক্ষতায় সামাল দিচ্ছেন। একই সঙ্গে চলমান রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় ঘুরে ঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, বেড়ানোর নেশা, এবং সাহিত্যের নবীন প্রতিভা অন্বেষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা।
 কথাসাহিত্যিক হিসেবে শ্রদ্ধেয় অমর মিত্রের আজকের যে অর্জন, সেটা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের ফলাফল। রাতারাতি এ সফলতা যেমন আসেনি, ফুৎকারে উবেও যায়নি। সক্রেটিসের বিখ্যাত বয়ান,‘সদগুণই জ্ঞান (Virtue is knowledge) আর জীবন একটা শিল্প(art)।’ এর প্রতিফলন দেখা যায় লেখক অমর মিত্রের জীবনাচরণে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি আপামর পাঠকের পাঠ তালিকায় উঠে গিয়ে দারুণভাবে তাঁকে জনপ্রিয়তার তকমা না দিলেও তিনি বহু সাধারণ এবং বোদ্ধা পাঠকের আরাধ্য লেখক। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত যেমনটা বলেছিলেন, “নীরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় কবি, জনপ্রিয়তার কবি নন।” অমর মিত্র সম্পর্কেও এ কথাটা খাটে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ অমর মিত্রের লেখালিখি। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য,
কথাসাহিত্যিক হিসেবে শ্রদ্ধেয় অমর মিত্রের আজকের যে অর্জন, সেটা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের ফলাফল। রাতারাতি এ সফলতা যেমন আসেনি, ফুৎকারে উবেও যায়নি। সক্রেটিসের বিখ্যাত বয়ান,‘সদগুণই জ্ঞান (Virtue is knowledge) আর জীবন একটা শিল্প(art)।’ এর প্রতিফলন দেখা যায় লেখক অমর মিত্রের জীবনাচরণে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি আপামর পাঠকের পাঠ তালিকায় উঠে গিয়ে দারুণভাবে তাঁকে জনপ্রিয়তার তকমা না দিলেও তিনি বহু সাধারণ এবং বোদ্ধা পাঠকের আরাধ্য লেখক। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত যেমনটা বলেছিলেন, “নীরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় কবি, জনপ্রিয়তার কবি নন।” অমর মিত্র সম্পর্কেও এ কথাটা খাটে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ অমর মিত্রের লেখালিখি। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য,
“আমি আমার যাপিত জীবনের বাস্তবতা নিয়ে বাঁচি। আমি যখন লিখতে বসি সেই বাস্তবতা থেকে যাত্রা করি অন্য কোনো বাস্তবতার সন্ধানে। এই সন্ধানটিই মূল সূত্র। অনেকক্ষেত্রে, বিশেষত গল্প রচনার ক্ষেত্রে, অনেক সময় আমাকে যাত্রা করতে হয় প্রায় শূন্য থেকে। সেখান থেকে পৌঁছতে চাইতে হয় এমন কোনো জায়গায়, যা ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এই অচেনা সত্যটি খুঁজে বের করাই কি লেখকের কাজ? অচেনা বাস্তবতা? আসলে সেই সত্য খুব কাছেরই সত্য, কিন্তু তাকে চেনা সম্ভব হয় না বলেই সব গল্প, গল্প হয়ে ওঠে না, সব সত্য, সত্য হয়ে ওঠে না। আমার খুঁজে পাওয়া সত্যের ভিতরে দূর ভারতবর্ষের কোনো এক গ্রাম্যবধূ তাঁর জীবনের সত্য খুঁজে পেয়ে যাবেন মনে মনে।”
এখানে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি বক্তব্য মনে পড়ছে, প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় সেটি উল্লেখ করতে চাই:
‘অন্যের কথা বলতে পারব না, আমার নিজের কাছে মনে হয় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার অভিজ্ঞতা পরিব্যাপ্ত নয় তার পক্ষে গল্পের অঞ্চলে বেশিদূর যাওয়াটা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। গল্পের আকর্ষণটা তখন আর তীব্র হয় না। গল্পে আকর্ষণ তৈরির জন্য বাস্তব জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যে কারণে বিমূর্ত একটি গল্প যখন কেউ ছাপান তখন সেটি পড়ে পাঠক খুব আনন্দ পান বলে মনে হয় না। বিমূর্ত গল্পও লেখা যায়, শিল্পের একটা অঞ্চলে বাস্তবকে অস্বীকার করে গল্প লিখা সম্ভব— সেরকম গল্প লেখাও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু আমি যে ধরনের গল্প লিখি সেখানে বাস্তব থেকে যদি খুব দূরে চলে যাই তাহলে মানুষ ভাববে ওই গল্পে কোনো অংশগ্রহণ নেই। এখানে বিপরীত কোনো চিত্র আমার থেকে এসেছে। আমি একটা ব্যাখ্যা দেই— একটা মুক্তা, তার ভেতরে যদি বালির দানা না থাকে তাহলে কিন্তু মুক্তাটা মুক্তা হয়ে উঠবে না। বালির দানাটা বাস্তব, মুক্তাটা হচ্ছে গল্প। আর বাস্তবতার ওপর, তার চারদিকে কল্পনার, এমনকি অলীক ভাবনার ঘেরাটোপ দিলেও গল্পের জীবনসত্যটা আড়াল পড়ে না, অনেক আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় বরং।’
 এমন পরিব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার নিবিড় চর্চা আমরা অমর মিত্রের সাহিত্যে বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। সাহিত্যের সত্যে পৌঁছাতে তিনি যে বাস্তবতা নির্মাণ করেন তাতে মিশে থাকে অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নানামুখী, একই সঙ্গে বৈচিত্রময়। শহুরে বা গ্রামীণ জীবনের ঘাত–প্রতিঘাত, বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে নিরন্তর যুঝতে থাকা জীবন, সুদিন কিংবা আধুনিকরণের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের নির্মমতা, অমানবিকতার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো মানবিকতা ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসে সহজাত স্বাচ্ছন্দ্যে ওঠে আসে। লোকজ বা ঐতিহাসিক কাহিনি অথবা মিথ সমান্তরালে তাল মিলিয়ে তাঁর অনেক উপন্যাসেই বর্ণিত হতে দেখা যায়। ইতিহাস, লোককথা বা মিথের, সেসব কাহিনি গড়িয়ে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মিশে যায় দারুণ বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে। দু’হাজার বছরের ইতিহাস উজিয়ে উজ্জয়িনী নগর ভীষণ জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসে। একই ভাবে ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড মহারাষ্ট্রের লাতুর কিল্লারি কিংবা গৌতম বুদ্ধের ঘোড়া, ব্যাবিলন, কারবালা, ময়ূরপাহাড়, আরারাত পাহাড়, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি নানা পটভূমিকে উপজীব্য করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের উপস্হিতি চোখে পড়ে অমর মিত্রের অনেক উপন্যাসে।
এমন পরিব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার নিবিড় চর্চা আমরা অমর মিত্রের সাহিত্যে বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। সাহিত্যের সত্যে পৌঁছাতে তিনি যে বাস্তবতা নির্মাণ করেন তাতে মিশে থাকে অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নানামুখী, একই সঙ্গে বৈচিত্রময়। শহুরে বা গ্রামীণ জীবনের ঘাত–প্রতিঘাত, বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে নিরন্তর যুঝতে থাকা জীবন, সুদিন কিংবা আধুনিকরণের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের নির্মমতা, অমানবিকতার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো মানবিকতা ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসে সহজাত স্বাচ্ছন্দ্যে ওঠে আসে। লোকজ বা ঐতিহাসিক কাহিনি অথবা মিথ সমান্তরালে তাল মিলিয়ে তাঁর অনেক উপন্যাসেই বর্ণিত হতে দেখা যায়। ইতিহাস, লোককথা বা মিথের, সেসব কাহিনি গড়িয়ে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মিশে যায় দারুণ বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে। দু’হাজার বছরের ইতিহাস উজিয়ে উজ্জয়িনী নগর ভীষণ জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসে। একই ভাবে ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড মহারাষ্ট্রের লাতুর কিল্লারি কিংবা গৌতম বুদ্ধের ঘোড়া, ব্যাবিলন, কারবালা, ময়ূরপাহাড়, আরারাত পাহাড়, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি নানা পটভূমিকে উপজীব্য করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের উপস্হিতি চোখে পড়ে অমর মিত্রের অনেক উপন্যাসে।
বর্তমান আলোচনা যে উপন্যাসটি ঘিরে তার আখ্যানেও ঘটেছে ইতিহাস আর মিথের উপস্থিতি। সমান্তরালে বর্ণিত হয়েছে বাস্তব জীবনের বয়ান। উপন্যাসের নাম “ও আমার ইচ্ছাপুর”। ইসলামের ইতিহাসে এবং হিব্রু বাইবেলে নূহের নৌকার একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। নূহের নৌকার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার আদেশে নূহ (আঃ) মহাপ্লাবণের হাত থেকে পৃথিবীর প্রাণীকূলকে রক্ষা করেন। বাইবেলের বর্ণনায় যেটিকে ‘নোহা’স আর্ক’ হিসেবে বলা হয়েছে। ইতিহাসের এই কাহিনির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অমর মিত্র তাঁর সহজাত দক্ষতায় জুড়ে দিয়েছেন বাস্তবের কাহিনি। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে উপন্যাসের একটি চরিত্র ইতিহাস বা মিথের সেই গল্প বলে যায়। আখ্যান গড়াতে থাকে বাস্তব আর মিথের হাত ধরে।
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীমূত বাহনের বিশ্বাস, নূহনবী “ইচ্ছাপুর হয়েই আরারাত পর্বতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।” কেননা এই গল্প শুনতে শুনতেই জীমূত বাহন বেড়ে উঠেছে। যা তার মনে অটল বিশ্বাস তৈরি করেছে। ইচ্ছাপুরে যেসব মুসলমান এবং খ্রিস্টান বাসিন্দা আছে তারা বলে, “তাঁদের পূর্বপুরুষ নূহের নৌকা থেকেই পছন্দপুরে নেমেছিল,… সৃষ্টির সেই আদিম যুগে।” যেহেতু ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত “মানুষ নেমেছিল নূহর নৌকা থেকে তাই পছন্দপুর এত সুন্দর।” আর সেই সুন্দরের জপ জলের মতো ঘুরে ঘুরে করে যায় জীমূত বাহন। যাকে এড়াতে পারেন না উপন্যাসের আরেক কেন্দ্রীয় চরিত্র জীমূত বাহনের মনোযোগী শ্রোতা নিলয় ঘোষ। চাকরি সূত্রে নিলয় ঘোষ এসেছিলেন ন’পাহাড়ি অঞ্চলে। তখন জীমূত বাহন ন’পাহাড়িতে স্কুলের ক্লার্ক। মাধ্যমিক পাশ জীমূত বাহন, বলে বি.এ পাশ। অথচ সার্টিফিকেট দাখিল করা সম্ভব হয়নি। কারণ পছন্দপুরে এক ঝড়ে সেটা উড়ে গেছে। তবে জীমূত বাহনের বিশ্বাস সার্টিফিকেট সে কোনো একদিন ঠিকই ফিরে পাবে। ইচ্ছাপুরের পক্ষে সবই সম্ভব। সে যেমন নেয়, ফিরিয়েও দেয়; এমন অসম্ভব কথা দারুণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে জীমূত বাহন। যা হেডস্যার সুপ্রকাশ বাবু গাঁজাখুরি বলে হেসে উড়িয়ে দিলেও নিলয় ঘোষের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয় না। নিলয় ঘোষ বিশ্বাস–অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে আটকে থাকেন। পছন্দপুরের অলৌকিক গাল–গল্পে বিভ্রান্ত নিলয় ঘোষকে মাধ্যমিক পাশ জীমূত বাহনের জ্ঞানের পরিধি ভীষণ বিস্মিত করে।
জীমূত বাহনের পা ন’পাহাড়ির মাটিতে থাকলেও তার মন পড়ে থাকে পছন্দপুর নামের এক অপার্থিব সুন্দর গ্রামে। যেখানে
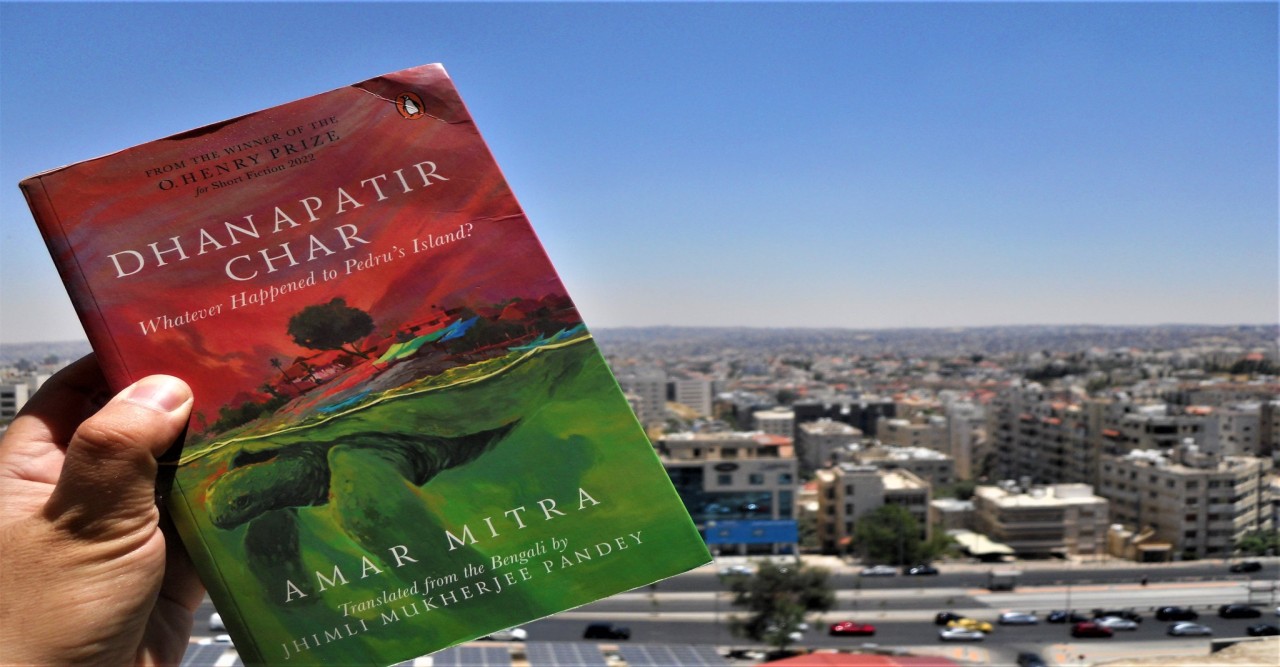 সে নিলয় ঘোষ কে নিয়ে যেতে চায়। ঘুরেফিরে তাদের কথোপকথনে পছন্দপুরের নাম উঠে আসে। ভক্তিসঙ্গীতের মতো জীমূত ভক্তিতে গদগদ হয়ে শোনায় সে গল্প। অলীক গল্প যেন, কারণ পছন্দপুরের কোনো জীর্ণতা নেই– টান টান সজীবতা আর পৃথিবীর তাবত সৌন্দর্য–ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রাম। কোনো দুঃখ–জরা কিংবা অভাব অনটন স্পর্শ করে না পছন্দপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। প্রকৃতিমাতার আর্শিবাদ পুষ্ট পছন্দপুরে আগেভাগে বর্ষা আসে। অন্য কোথাও কাশ ফুল ফোটার আগে কাশফুল ফোটে। ধানের থোড়ে দুধও আসে সময়ের আগে। খেজুর গাছে রস, পলাশ গাছে ফুল সেসবও এসে যায় বেশ আগে। পুরোমাত্রায় স্বপ্নলোক পছন্দপুর। কোনো মলিনতা আঁচড় বসাতে পারে না পছন্দপুরের গায়ে। কঠিন বাস্তবতা শুধুমাত্র ন‘পাহাড়ি অঞ্চলে তার কাটাকুটির চিহ্ন রেখে যায়। সেই চিহ্ন স্হানীয় বাসিন্দাদের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয়। ভাত–কাপড়ের জন্য তাদের নিরন্তর লড়াইয়ের চালচিত্র ফুটে ওঠে তাদের নানান আচার অনুষ্ঠানে। ভাদ্রসক্রান্তিতে তারা যে গীত গলায় তুলে নেয়– তাতে বাস্তবতার রূঢ়তা লেপ্টে থাকে…
সে নিলয় ঘোষ কে নিয়ে যেতে চায়। ঘুরেফিরে তাদের কথোপকথনে পছন্দপুরের নাম উঠে আসে। ভক্তিসঙ্গীতের মতো জীমূত ভক্তিতে গদগদ হয়ে শোনায় সে গল্প। অলীক গল্প যেন, কারণ পছন্দপুরের কোনো জীর্ণতা নেই– টান টান সজীবতা আর পৃথিবীর তাবত সৌন্দর্য–ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রাম। কোনো দুঃখ–জরা কিংবা অভাব অনটন স্পর্শ করে না পছন্দপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। প্রকৃতিমাতার আর্শিবাদ পুষ্ট পছন্দপুরে আগেভাগে বর্ষা আসে। অন্য কোথাও কাশ ফুল ফোটার আগে কাশফুল ফোটে। ধানের থোড়ে দুধও আসে সময়ের আগে। খেজুর গাছে রস, পলাশ গাছে ফুল সেসবও এসে যায় বেশ আগে। পুরোমাত্রায় স্বপ্নলোক পছন্দপুর। কোনো মলিনতা আঁচড় বসাতে পারে না পছন্দপুরের গায়ে। কঠিন বাস্তবতা শুধুমাত্র ন‘পাহাড়ি অঞ্চলে তার কাটাকুটির চিহ্ন রেখে যায়। সেই চিহ্ন স্হানীয় বাসিন্দাদের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয়। ভাত–কাপড়ের জন্য তাদের নিরন্তর লড়াইয়ের চালচিত্র ফুটে ওঠে তাদের নানান আচার অনুষ্ঠানে। ভাদ্রসক্রান্তিতে তারা যে গীত গলায় তুলে নেয়– তাতে বাস্তবতার রূঢ়তা লেপ্টে থাকে…
ভাদর মাসে ভাদু আন্যে
ভাদু পূজা দায় হল্য
টাকা দিয়া চাল মিলে না
লাপসি খায়ে দম গেল।
আর জীমূত বাহনের পছন্দপুর আহ্লাদে ছমছম করে সেখানে গেয়ে ওঠে–
আমার ভাদু সুনার মেয়ে
সুনার বরণ তার,
একবার সে হাসে যদি,
সূয্যি পিবের ধার।
পছন্দপুরের ভাবালুতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা জীমূত বাহনের বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলে,জীবন জীবিকার জন্য তাকে ন‘পাহাড়িতেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্য চশমার সাহায্য নিতে হয়, তার ভাষ্য থেকে জানা যায় পছন্দপুর ফিরে গেলে তার আর চশমার দরকার হবে না। পছন্দপুর এমনই জাদুময় এক স্হান। অন্যদিকে, চাকরি সূত্রে নিলয় ঘোষের ন‘পাহাড়িতে যাওয়া। পরে চাকরি বদল করে ফিরে আসেন কলকাতা– নিয়ম মতো একসময় চাকরি থেকে অবসর নেন। কলকাতার কাছে নিউ টাউনে তার ফ্ল্যাট। কোঅপারেটিভের সাহায্যে সেটা করা সম্ভব হয়। একাই থাকেন নিলয়।তার জীবনে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে…পালিতা একমাত্র কন্যা সন্তান বাবলিকে হারান প্রথমে– সন্তান বাবলির শোকে নির্বাক স্ত্রী শতরূপাও চলে যান তিন বছরের মাথায়। ‘৪৩ এর মনন্তরে নিলয়ের পূর্বপুরুষ পুরুলিয়ার (আগে ছিল মানভূম পরে পুরুলিয়া নামকরণ হয়) প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। নিলয় সেই মর্মান্তিক সময়ের গল্প শুনেছেন বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে। তার বেড়ে ওঠা কলকাতার এক আধাবস্তিতে। জীবনের নির্মমতার পাঠ হাড়েহাড়ে টের পাওয়া মানুষ নিলয়। মেধাবী ছিলেন, সে কারণে আধাবস্তির অন্ধকার পরিবেশের থাবায় তাকে পড়তে হয়নি। মেরেকেটে জীবনে দাঁড়িয়ে গেছেন।
জীমূত বাহনের পছন্দপুরের গল্পে নিলয়ের পুরোপুরি আস্হা না থাকলেও নীরব শ্রোতা হিসেবে শুনে যেতেন— শুনতেন বলেই না জীমূত অত কথা কইতো। তার নিউ টাউনের অবসরকালীন জীবনে বহু বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে জীমূত বাহন ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তার সাথে আবারও যোগাযোগ স্হাপন করে। ফোনালাপের সূত্রে আবার তাদের কথোপকথন শুরু হয়। ফোনালাপেও নিলয় শ্রোতা, মূল বক্তা জীমূত, বক্তব্যের কেন্দ্রীয় বিষয় ‘পছন্দপুর’। জীবনের এই পর্বে নিঃসঙ্গ নিলয় জীমূতের ফোনের অপেক্ষাতে যেন উদগ্রীব থাকতেন। মনোযোগী শ্রোতা হয়ে শুনতেন জীমূতের নানান ব্যক্তব্য।
এমন হতে পারে জীমূতের গল্পের সুতো ধরে তিনি নিজেও অলীক সেই পছন্দপুরে পৌঁছাতে চাইতেন। কঠিন বাস্তব থেকে বাঁচতে মন ভোলানো অলীক কল্পনায় ডুবে যাওয়ার ছুতো মানুষ খুঁজে পেতে চায় বৈকি! তাছাড়া এমন গল্পে নিলয় অভ্যস্ত। নিলয়ের মা’ও মানভূমের গল্প করতেন। মানভূমের গ্রাম মুলুকের মেয়ে ছিলেন তিনি। যে গ্রামে ১৩৫০ সনের আগে কোনো অভাব অনটনের নাম নিশানা ছিল না। সুখের নহরে ভাসতো মুলুক নামের গ্রাম। যেমনটা ভাসে জীমূত বাহনের পছন্দপুর।
জীমূত বাহনের ‘পছন্দপুর’ আমাদের মনে করিয়ে দেয় বুড়ো পর্যটক নাবিক রাফায়েল হাইথ্লডের (Raphael Hythloday) কথা। এটি স্যার থমাস মুরের ‘ইউটোপিয়া (Utopia)’এর একটি চরিত্র। ‘ইউটোপিয়া’ থমাস মূর রচিত কল্পনাপ্রসূত একটি উপন্যাস। যাকে সব পেয়েছি’র দেশ বা মায়ানগরীও বলা যায়। ভ্রমণ কাহিনির মাধ্যমে এক স্বপ্নলোকের
গাল–গল্প ইউটোপিয়া। সেসময় ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরি। রাজার দূত হিসেবে থমাস মুর বাণিজ্য বিষয়ে আলাপ–আলোচনার জন্য নেদারল্যান্ড গিয়েছিলেন। ফেরার পথে অ্যান্টওয়ার্প(Antwerp) ভ্রমণ করেন। সেখানে পিটার গিলস্ নামে এক প্রাজ্ঞ লোকের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। গিলসের মাধ্যমে মুরের পরিচয় ঘটে ভ্রমণ প্রিয় নাবিক রাফায়ে হাইথ্লডের সঙ্গে।
‘ইউটোপিয়া’ উপন্যাসের এই ভ্রমণপ্রিয় নাবিক, দার্শনিক চরিত্রের মাধ্যমে থমাস মুর পাঠককে এক অলীক দ্বীপ দেশের গল্প শোনান। রাফায়েল পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। সেরকম এক ভ্রমণে বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci) এর সঙ্গী হয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দক্ষিণে এক দ্বীপদেশে গিয়েছিলেন রাফায়েল। যে দেশটিকে তিনি ‘ইউটোপিয়া’ নামে আখ্যায়িত করেন। শিক্ষিত, বিচক্ষণ, এবং মানবতাবাদী শাসক সে দেশ শাসন করেন। যেখানে শ্রমের সুষম বন্টনের রীতিতে স্হায়ী জনগণ অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত সম্পদের বালাই ছিল না, রাষ্ট্রীয় সম্পদে ছিল সবার সমান অধিকার। অর্থাৎ কল্পনায় মানুষ যেরকম আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি আঁকতে ভালোবাসে ঠিক সেরকম এক দেশ ইউটোপিয়া। যে দেশে মানুষের জীবন ব্যাপক রকমের সুখের।
‘ইউটোপিয়া’ এক স্বপ্নালোক। স্বপ্নলোকের চাবি কেউ কখনও খুঁজে পায় না; পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেরকম কোনো দেশ পৃথিবীর কোথাও নেই। যা বাস্তবে নেই কল্পনার হাতে ধরে সেখানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। থমাস মুর কল্পনার হাত ধরে সেরকম এক দেশের গল্প রচনা করেন ১৫১৬ সালে। কেন এমন অবাস্তব এক দেশের গল্প তিনি রচনা করলেন সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ইংল্যান্ড তথা তৎকালীন ইউরোপের সামাজিক–রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। সে সময় ইংল্যান্ড বা ইউরোপে শাসনচর্চা ছিল চরমরকম শোষণের। সম্পদের প্রায় সবটাই ছিল ক্ষমতাশালীদের কুক্ষিগত। সাধারণ মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে কোনো রকমে জীবন কাটাতো। অন্যদিকে অঢেল বিলাসব্যসনের পেছনে অপচয় ঘটাতো রাজকোষাগার। রাজতন্ত্র আর ক্যাথলিক গির্জার মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে যে রেষারেষি তার আঁচ কম–বেশি জনগণের উপরও এসে পড়তো। মোট কথা, উপরে উপরে চাকচিক্যের খোলস থাকলেও আদতে সে বড় সুখের সময় ছিল না। ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের সামাজিক এবং আর্থ রাজনৈতিক পরিস্হিতিকে ব্যঙ্গ করে প্রাজ্ঞ স্যার থমাস মুর ওরকম একটা উপন্যাস রচনা করেন।
সপাটে যখন রূঢ় সত্যিটা বলা সম্ভব হয় না তখন ঘুরিয়ে বা আড়াল নিয়ে বলতে হয়। ভৈরব হাজারিরা ঘুরে ফিরে ক্ষমতার বলয়ে আসীন হয় যুগে যুগে। তাদের বিরুদ্ধে সপাটে রুখে দাঁড়াতে না পারার বেদনা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যেই হয়ত পছন্দপুর নামের ইউটোপিয়ার জন্ম। জীমূত বাহনের মতো ক্ষমতাহীন, অসহায় মানুষেরা অনেক সময় স্বপ্নের ভিতর বাঁচতে চায়। কল্পনাকে আশ্রয় করে তৈরি করতে চায় এক মায়ানগরী। যে নগরীর মাথার উপর ঈশ্বরের হাত থাকে তাকে তো পৃথিবীর ক্ষমতালোভীরা গিলে খেতে কিছুটা ভয়ই পায়। মন ভোলাতে এই ছেলেমানুষি। গালিবের বিখ্যাত সেই লাইন কেমন মূর্ত হয়ে ধরা দেয় জীমূত বাহনের আচরণে– “স্বর্গের সত্যি–মিথ্যা আমার বেশ জানা আছে, কিন্তু মন কে ভোলাতে অলীক কল্পনাটা মন্দ কী!”
জীমূত বাহনের পছন্দপুর এক ইউটোপিয়া বিশেষ। বিপরীতে বাস্তবের ন’পাহাড়ি ডেসটোপিয়ার (Dystopia) চূড়ান্ত উদাহরণ। যেখানে নিরন্তর চলে সাধু আর শয়তানের যুযুৎসু। ক্ষমতাবান যাকিছু সুন্দর পার্থিব, সেগুলো কুক্ষিগতের জন্য হাত বাড়ায়। শ্রেণিভেদের দেয়াল তুলে কেড়ে নেয় ভালোবাসার অধিকার; হত্যাকাণ্ড কে হালালের অনুশীলন চালায়। ভৈরব হাজারি দশ মাথার দানব হয়ে সব গিলে খেতে চায়। ভাত–কাপড়ের জন্য যেখানে সাধারণ মানুষকে নিরন্তর লড়াইয়ের সামিল হতে হয়। শপিংমল আর বিলাসী জীবনের মোহে ক্ষমতাশালীর লোলুপ থাবা হজম করতে থাকে পাহাড় থেকে– সমতলভূমি। অগ্রগতির নামে গ্রামীণ সারল্য খাবলে খেয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় কলকারখানা– যার বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার আস্তরণে চাপা পড়ে যায় গ্রামের সবুজ শ্যামল প্রাণবন্ত শোভা। ভৈরব হাজারি, বা ভি. হাজরা অথবা কালভৈরবি দশমাথার দানব হয়ে কখনো কৃষ্ণচন্দ্রের রক্তে হাত রাঙায়, কখনো শিল্পা আর তার স্বামীর। অপরাধীর নাম আর স্হানের বদল ঘটে কেবল, খুনীর লক্ষ আর ক্ষমতা কুক্ষিগতের লোভ একই রকম চেহারা নিয়ে সামনে আসে। ভুগতে হয় ক্ষমতা নিয়ে মাথাব্যথাহীন মানুষদের। এইসব দমচাপা বাস্তবের মাঝে দাঁড়িয়ে জীমূত বাহন হাঁসফাঁস করে। মায়ানগরী ‘পছন্দপুর’ হয়ে তখন তাকে দু’দণ্ড শান্তি জোগায়। নিলয় ঘোষ কে পছন্দপুরের গল্প শুনিয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে সে নিজেকেই শোনায় সেই অলোকপুরীর গল্প। ইথারে ইথারে ভাসিয়ে দেয় প্রিয় সেই ভূমির ঘ্রাণ।
যে মাটিতে মানুষ জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, সেই স্থান তার কাছে সবচে’ প্রিয়। প্রিয় সেই দেশ কিংবা গ্রামকে মানুষ বুকে বহন করে বেড়ায়। জীবন জীবিকার তাগিদে নাড়ীপোতা জায়গা ছাড়তে হলেও প্রিয় স্থানকে মানুষ সযত্নে বুকের খাঁজে রাখে। সময় সময় তার বন্দনায় মগ্ন হয়। পৃথিবীর তাবত স্থান, প্রিয় সেই জায়গার কাছে মলিন, প্রাণহীন। সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে’র আবদুর রহমান সুযোগ পেয়ে বুকের ভাঁজ খুলে তার জন্মস্থান পানশির কে লেখকের সামনে তুলে ধরে। পানশিরের প্রশংসায় মুখর হয়। আবদুর রহমানও ঠিক জীমূত বাহনের ভঙ্গিতে লেখক কে শুনিয়ে ছিল উত্তর আফগানিস্থানে অবস্থিত তার জন্মস্হান পানশিরের অবাক গল্প। “আমার দেশ– সে কী জায়গা!একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢােক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তেজি ঘােড়ার সঙ্গে বাজি রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তাে পায়ে হেঁটে চলে , বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।” আবদুর রহমান গভীর ভালোবাসায় উচ্চারণ করেছিল – ইনহাস্ত ওয়াতানাম! একই আকুতির প্রতিধ্বনি ভেসে আসে আভার বিখ্যাত কবি রাসুল গামজাতভের (Rasul Gamzatovich Gamzatov) ‘আমার জন্মভূমি দাগেস্তান’এর পাতা ফুঁড়ে, “অদৃষ্ট আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক, আমি নিরন্তর নিজেকে আমার মাটির, পর্বতরাজীর এবং যে গ্রামে আমি প্রথম ঘোড়ায় জিন লাগাতে শিখেছি, সেখানকার প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেকে অনুভব করি। যেখানেই থাকি, আমি নিজেকে আমার জন্মভূমি দাগেস্তানের বিশেষ দূত হিসেবে গণ্য করি।”
জীমূত বাহনও পরম ভালোবাসায় নিরন্তর বলে গেছে পছন্দপুরের কথা। তার মুখে দিনের পর দিন পছন্দপুর নামের অনিন্দ্য সুন্দর গ্রামের গল্পের শ্রোতার তালিকায় একে একে জুড়ে যায় নিলয়ের এক বন্ধু আর প্রতিবেশি। অনিমেষ এবং রামচন্দ্র। তারা পছন্দপুরে যেতে ভীষণ আগ্রহী। জীমূতের গল্পে পছন্দপুরের চরম প্রশংসার পাশাপাশি ন’পাহাড়ির বাস্তবতাও উঠে এসেছে। সে বর্ণনার সাথে রামচন্দ্রের জন্মস্হান মহারাষ্ট্রের লাতুরের ভীষণ মিল। কাল ভৈরব সেখানে ভৈরব হাজরার পরিবর্তে, এইটুকু যা তফাৎ, বাকি কাহিনি একই বঞ্চনার–যন্ত্রণার আর দাপটের। সেখানে যাওয়ার আগ্রহ নেই রামচন্দ্রের। সে স্বপ্নলোক পছন্দপুরে যেতে চায়। আর নিলয় ঘোষ আগে তার ফেলে আসা ন’পাহাড়িতে যেতে চান। জীমূতের মুখে ন’পাহাড়ির রূপান্তরের কথা জানতে পেরে নিলয় ঘোষের ভিতর ন’পাহাড়ির বদলে যাওয়া অবয়ব কতটা অচেনা হয়েছে সেটা নিজ চোখে দেখার তীব্র ইচ্ছা জাগে। তাই সরাসরি পছন্দপুর নয়, ন’পাহাড়ি যাবার জন্য তিনি উতলা। তিনি জানতে ইচ্ছুক ন’পাহাড়ির বাতাসে বর্তমানে কতটা সিলিকা ভাসছে। জীমূতের বলা ন’ পাহাড় ভেঙে ছয় পাহাড়ের এখন কতটা অবশিষ্ট আছে? পাহাড়ের বুক–পাঁজর ভাঙা পাথর কোন কোন নগর সাজাতে পাঠানো হচ্ছে? কতটা বুড়ি হয়েছে নিলয় ঘোষের সুন্দরী প্রিয়তমা? ভাইহারা রামচন্দ্র, কৌতূহলী নিলয় ঘোষ অনেক প্রশ্ন মুঠো ভরে পছন্দপুর কিংবা ন’পাহাড়ির দিকে যাত্রা করে। বাতাস বুঝি ফিসফিসিয়ে ওঠে – “এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া।” এই ভ্রমণের গন্তব্য পছন্দপুর নামের মায়ানগরীতে গিয়ে মিশেছিল কিনা। কোন সত্যের মুখোমুখি হতে হয় তাদের সে গল্পটুকু
“ও আমার পছন্দপুর” উপন্যাসের আগামি পাঠককের জন্য তোলা রইল।
বাস্তব, পরাবাস্তব বা জাদুবাস্তবের মিশেলে লেখা “ও আমার পছন্দপুর” পাঠ পাঠকের জন্য নিঃসন্দেহে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। শ্রদ্ধেয় অমর মিত্রের পেন্সিল সোনার অক্ষরে আরো বহুদিন লিখে যাক সেই শুভকামনা।










.jpeg)
.jpg)